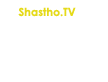মতামত ও বিশ্লেষণ
সাতকানিয়ার চুপচাপ বালক যেভাবে হয়ে উঠেন কিংবদন্তি চিকিৎসক

আজ থেকে ৬৬ বছর আগে এই দিনে সাতকানিয়া উপজেলার কাঞ্চনা উনিয়নের মৌলভি বাড়ি নামের এক গ্রামে ঈদ উদযাপনের প্রস্তুতি হচ্ছিল। আর ঠিক ঈদের দিন সকালে বেগম আমাতুন নুর আর মোহাম্মাদ মোনিরুল হকের বাড়িতে এসে পড়ল তাদের ৬ষ্ঠ সন্তান। বিভিন্ন কারণে বাচ্চাটা হয়ে উঠল তার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। ভালবেসে নাম রাখা হলো রিজওয়ান, ডাকনাম রিজু।
মসজিদের ইমাম পরে আদেশ করল যে, রিজওয়ান আরবিতে ঠিক হয় না, আসল নাম হওয়া উচিত রিদওয়ান যেভাবে কোরআনে এসেছে কথাটা। কিছু ট্রেডিশানে বলা হয় যে, রিদওয়ান হলো সেই ফেরেস্তার নাম যে বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, সেই সূত্রেই এই নাম। তাও ডাকনামটা গেল না, আশপাশের সবাই রিজু বলেই ডাকতো। ছোট, চুপচাপ আবার দুষ্টু এই ছেলে জীবনের প্রথম ১৬ বছর কাটিয়েছিল কাঞ্চনাতেই। লোকাল প্রাইমারির পর হাই স্কুল ছিল একেবিসি ঘোষ ইনস্টিটিউটে- কাঞ্চনার হাই স্কুল। এসএসসি পাস করে কুমিল্লা বোর্ড থেকে।
বড় ভাই ড. খালিকুজ্জামানের আদেশে ইন্টারমিডিয়েট করতে যায় ঢাকায়। এমন এক ছোট গ্রাম থেকে হঠাৎ ঢাকা পৌছায় কিছুটা শক খেয়ে যায়। রেজাল্ট দেরিতে আশায় ভর্তি হয় আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে। চুপচাপ ছেলেটা আরো একটু চুপচাপ হয়ে যায়, কথা বলতে গেলেই চিটাংগা কথা বেরিয়ে আসত। অপরদিকে ক্লাসের অনেকেই ছিল পাকিস্তানফেরত ইংরেজি বলা স্টুডেন্ট। বড় ভাই শিখিয়েছিল ইংরেজির গুরুত্ব। প্রতিদিনের বাংলাদেশ অবর্জাভার (Bangladesh Observer) পত্রিকা পড়তো, সাথে একটা ডিকশনারি (dictionary) হাতে নিয়ে। যেই শব্দ অপরিচিত সেটা পড়ে নিবে ডিকশনারি থেকে। এভাবে করতে করতে এইচএসসি পাশ করে ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে।
এরপর হয় মজার ঘটনা। প্রথমে চান্স পেয়েছিলেন বুয়েটে। ফর্ম ও ফিলআপ করা শেষ। কিন্তু মা, বাবা ও বড় ভাইরা বলেছিল যে, ৭ ভাই-বোনের একজন ডাক্তার হলে হয়ত ভাল হয়। এই এক সিদ্ধান্তে পাল্টে যায় তার ও আশপাশের সবার দুনিয়া। বুয়েট ছেড়ে মেডিকেলে ভর্তি হয়, চান্স হয়ে যায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক)। চমেকে এসে তার একটা রেপুটেশান হয়ে যায়। কেউ তেমন পড়ালেখা করতে দেখত না। কিন্তু পরীক্ষার সময় আসলেই পাস করে যেত, আর সব সাবজেক্ট নিয়ে ছিল খুব ডিপ নলেজ। কারণ, মেডিকেলের পড়া পরীক্ষার পড়া ছিল না, ছিল একটা প্যাশান। মেডিকেলের বইগুলো পড়ত গল্পের বইয়ের মত, সারা বছর। এক টপিক পড়তো বিভিন্ন বই থেকে। তার পরীক্ষার আগের দিন সবাই যখন পড়তে পড়তে শেষ, তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুম। ফাইনাল প্রফেশানাল এক্সাম দেয়ার পর দ্বীতিয় পজিশানে স্ট্যান্ড করে। এ কারণে ঢাকার পিজি হাসপাতালে (এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) ইন্টার্ন করার সুযোগ পায়। পিজিতে আবার ফিরে আসবে পরে এফসিপিএস ট্রেনিংয়ের সময়।
পাস করার পর প্রায় এক যুগ সরকারি চাকরির সুবাধে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে অনেক সময় কাটিয়েছিল। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের একদম সিমান্ত এলাকায় পোস্টিং হয়েছিল প্রথম দিকে। ট্রেনিংয়ের জন্যে ঢাকা এসে আবার কনসাল্টেন্ট হওয়ার পরেও প্রথম পোস্টিং হয় খাগড়াছড়িতে। সেখানে দুইটা জিনিস হয়।
এই সময়ে ফ্যামিলির এরেঞ্জমেন্টে বিবাহ হয় সহধর্মিনি ডা. রাশেদা সামাদের সাথে, যে নিজেই হয়ে উঠে একজন অধ্যাপক ও অসাধারণ চিকিৎসক। দুইজনের প্রথম থাকা সেই খাগড়াছড়িতে। ব্যক্তিগত এই মাইলফলকের পর প্রফেশানাল এক মাইলফলক হয় যেটা নিয়ে হয়ত তেমনই ভাবেন ওই সময়। খাগড়াছড়ি এসে দেখেছিল যে শত শত রোগী প্রতি মাসে মারা যাচ্ছে ম্যালেরিয়ায়। আসলে কোন ট্রিটমেন্ট কার্যকর ও কোনটা না, সেটা নিশ্চিত ছিল না। নিজেই জীবনের প্রথম রিসার্চ করে। এই কাজে দেখা যায় দেশের ম্যালেরিয়ায় আছে ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্স। এই কাজটা পরে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার এক ভিজিটিং টিমকে দেখায়, যারা এ নিয়ে খুব ইমপ্রেসড হয়েছিল।
এই শুরু ম্যালেরিয়ার গল্প। ১৯৯৪ সালে নিজের মেডিকেল কলেজ চমেকে ফিরে এসে যোগ দেয়। এরপরের ৯টা বছর বের হয়ে আসে অন্য এক প্রতিভা – টিচিং। হাজার হাজার ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক হিসেবে স্থান পেয়ে নেয়। সেই ছাত্ররা নিজেরাই এখন সব বড় বড় অধ্যাপক। কিন্তু ম্যালেরিয়ার কাজ থামে না। অধ্যাপক আবুল ফয়েজের নেতৃত্বে কাজ শুরু হয় ম্যালেরিয়া রিসার্চ গ্রুপের। ওই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্যালেরিয়ার অবস্থা খুবই বাজে। একটার পর একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয় যেখানে প্রমান করানো হয় যে নতুন একটা ওষুধ অনেক বেশি কার্যকরি ম্যালেরিয়া ঠেকাতে। এই ওষুধের আবিষ্কারক, ডা ইয়ু ইহু টাহ, অনেক বছর পর এই আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পেয়েছিল। এই ওষুধের অধিকাংশ ট্রায়ালের সব চেয়ে বেশি রোগি রেজিস্টার করা হয় বাংলাদেশে। একটা পেপার ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের বেস্ট পেপার আখ্যায় পায় ২০১০ এ। তিনি ম্যালেরিয়ার কাজে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার ক্লিনিক্যাল মনিটর হিসেবে কাজ ও করেছেন তাঞ্জানিয়া, ঘানা ও জাম্বিয়াতে।
ম্যালেরিয়ার কাজ চলতে চলতে ২০০৩ সালে এ তাঁর ট্রান্সফার হয় ঢাকায়। কিছু সময় স্যার সালিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, কিছু সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের পর ২০০৬ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে স্থান পায় ২০০৬ সালে। এখানেই জীবনের শেষ ১১ বছর কাজ করেছিলেন, আর এই কর্মস্থল হয়ে উঠেছিল তার প্রিয় মেডিকেল কলেজ। রিটায়ারমেন্টের পরেও বলত ‘আমার মেডিকেল কলেজ’।
ঢাকায় এসে আরো অন্যান্য গবেষণার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। জীবনের শেষের দিকে ফোকাস মেইনলি হয়ে যায় নন-কমিউনিউক্যাবল ডিজেজ (এনসিডি) নিয়ে এবং মেডিকেল এডুকেশান। খুব চিন্তা করতো বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে- ভয় পেত যে সিস্টেম আউটডেটেড এখনের সিস্টেমে ভাল ডাক্তার ভাল শিক্ষক বের হতে হলে সিস্টেম পাল্টানো দরকার।
২০১০ থেকে ২০১৬ আরেকটা কাজে ব্যস্থ ছিল। ময়মনসিংহে ওই সময় কালাজ্বরে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। ড্রাগ ফর নেগলেকটেড ডিজিজ ইনিশিয়েটিভ (ডিএনডিআই) এর একটা প্রজেক্টে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার হিসেবে একটা নতুন ওষুধের ট্রায়াল চালু করেছিল। এই ট্রায়ালে বিশ্বব্যাপি গাইডলাইন পালটে যায় চিকিৎসার। কালাজ্বর চিকিৎ্সায় এসে পরে এক নতুন মাইলফলক। গত বছর তার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ এখন কালাজ্বর মুক্ত।
চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করলেও মন টা পরে থাকত দুই জায়গায়- বন্ধুবান্ধব, পরিবারও তার গ্রামে। প্রতিবছর একাধিকবার বিভিন্ন ট্যুর প্ল্যান করত বন্ধুদের, পরিবার নিয়ে। দেশ ও বিদেশে খুব ইউনিক কিছু জায়গায় নিয়ে যেত বড় বড় গ্রুপ, করত অসাধারণ অর্গানাইজেশান। আর নিজের গ্রাম নিয়ে সব সময় অনেক ভাবত। সবাই ছেড়ে চলে যাওয়া এই গ্রামকে কিভাবে আবার উজ্জ্বীবিত করবে তা নিয়ে অনেক ভাবতেন। ৩০ বছর দুই ঈদে রোগী দেখতেন ফ্রিতে। শীতে, গরমে, বর্ষায়- ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ফার্মেসির পিছনের ছোট রুমে বসে নিরলস রোগী দেখে যেত। মাঝে মাঝে একদিনে ৩০০ জনও দেখত। কখনো ক্লান্টি বা বিরক্তি দেখাতেন না। এর মাঝে ছিল অনেক অনেক দান- কাকে কখন কিভাবে দিয়েছে, সেটা বলত না কাউকে, হয়ে যেত সব গোপনে।
এই অসাধারণ ব্যক্তির ৬৬তম জন্মদিন হওয়ার কথা ছিল আজকে, কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে নেই। গত বছর জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি করলা, বলল আরে বুড়া মানুষের আবার কি জন্মদিন! দুইজন মিলে অনেক হাসাহাসি করলাম। মজা করে আমি বলেছিলাম, আরে বুড়া হলেই তো উপভোগ করবা, আর কয়টা আছে তো জানো না। আল্লাহ আর একটাও রাখে নাই, সেটাই ছিল শেষ। আপন পরিবারের বাইরেও বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্র ও কলিগদের মধ্যেই হয়ে উঠেছে আরেক বিশাল পরিবার। একজন কয়েক মাস আমাকে বলে- ‘তোমার ফ্যামিলি ইস্যুতে অন্যদের এত চিন্তা কেন?’ সে আসলে বুঝেনাই যে অধ্যাপক মো. রিদওয়ানউর রহমান নিয়ে ফ্যামিলি ইস্যু বলতে কিছু নাই। তার জীবন, তার কাজ, তার সব কিছু নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ভাবত এবং এখনও ভাবে। লিখতে থাকলে আরও অনেক পাতাই লিখা যেত, কিন্তু আজ এখানেই ইতি।
আল্লাহ যেন বেহেশতের দর্জায় রিদওয়ানের সাথে আমার বাবা রিদওয়ানের দেখা করিয়ে দেয়। আমরাও যেন একি রাস্তায় এক অন্য সময় আবার একে অপরের দেখা পাই, এমন এক জায়গায় যেখানে আর কষ্ট নাই, ব্যাথা নাই, হারানোর কিছু নাই৷ আছে শুধু অনন্তকাল ধরে শান্তি। আল্লাহ বাবাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সব চেয়ে উচু স্থানে একটা জায়গা করে দিন।
লেখক : ডা. রাইয়িক রিদওয়ান (অধ্যাপক ডা. রিদওয়ানুর রহমান এর ছেলে)
ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগ, লুটন এবং ডান্সটেবল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, যুক্তরাজ্য