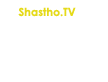প্রধান খবর
স্বাস্থ্য খাতকে নিরাপদ রাখতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ দরকার
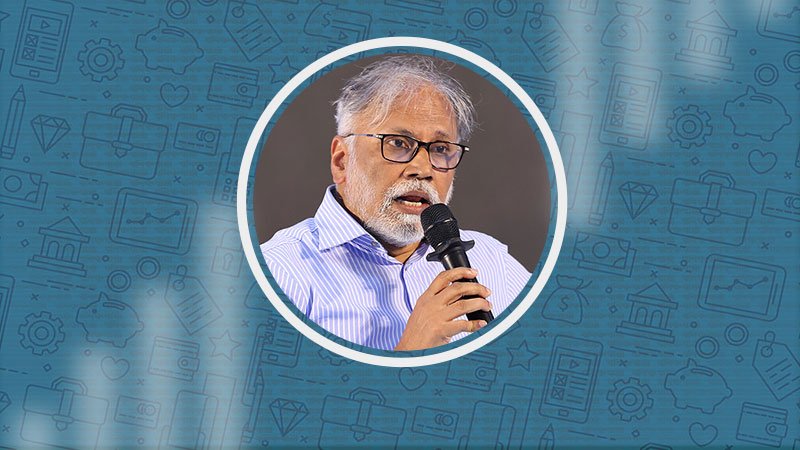
আমরা অল্পদিনের জন্য আসা একটি অন্তর্বর্তী সরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা স্বাস্থ্য খাতে যুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। এখানে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই।
আমরা অল্পদিনের জন্য আসা একটি অন্তর্বর্তী সরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা স্বাস্থ্য খাতে যুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। এখানে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। স্বাস্থ্য খাতের সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ছাড়া আমরা কোনো কাজ করছি না। কথা হলো, আলাপ-আলোচনা মানেই কারো মতকে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা বোঝায় না। মূলত পরিস্থিতি বোঝার জন্যই আলোচনা করা হচ্ছে। আমাদের কোনো কাজই নিয়ন্ত্রণমূলক নয়। রেগুলেশনে যদি কোনো খাত থাকে সেটি হলো স্বাস্থ্য।
রাষ্ট্রের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বাস্থ্যেও নিয়ন্ত্রণ সেভাবেই প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ বলে আমরা নিবর্তন কিংবা অত্যাচার বুঝি কিনা? নিয়ন্ত্রণ যদি নিবর্তন বা অত্যাচারের পর্যায়ে যায় তাহলে সেটি অবশ্যই আপত্তিকর। স্বাস্থ্য খাত নিরাপদ হওয়া দরকার। নিরাপদ হতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। তবে সেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যেন অত্যাচারী কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়, সেটিও লক্ষ রাখতে হবে। সেই নিয়ন্ত্রণ যেন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় করা হয়।
আমরা সরকারি-বেসরকারির পার্থক্য মুছে দিয়েছি। এখন থেকে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক অভিন্ন আইন মেনে চলবে। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবার এক মেট্রিক্সে মূল্যায়িত হবে। এতদিন এটি ছিল না। এতদিন এটি বায়বীয় ছিল। এখন আমরা এটি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করছি। একটি মেডিকেল কলেজ অবকাঠামো, শিক্ষক, গবেষণা ও ল্যাবরেটরির জন্য ১০০-এর মধ্যে কত স্কোর পাবে সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটির আলাদা স্কোর হবে। এটি স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্ধারণ করা হবে। এরপর ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্রেডিং করা হবে। এরপর সেটা ওয়েবসাইটে সরাসরি তুলে দেয়া হবে যাতে সবাই দেখতে পারে কোন মেডিকেল কলেজ এ, বি, সি কিংবা ডি গ্রেডের। এটি সরকারি ও বেসরকারি সব মেডিকেলের জন্যই প্রযোজ্য হবে।
এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, বাংলাদেশে কম্প্রোপ্রাইজ কোয়ালিটির চিকিৎসক তৈরি হলে কী পরিমাণ ঝুঁকি তৈরি করে। তিন বছর ডি ক্যাটাগরি হিসেবে পরিচালিত একটি মেডিকেল কলেজে ৩০০ চিকিৎসক তৈরি হলো এবং তারা যদি সারা জীবন তাদের সামনে আসা রোগীকে কম্প্রোমাইজ কোয়ালিটির চিকিৎসা দেয়, তাহলে রোগীরা অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। এ বন্দোবস্তগুলো সারা বিশ্বেই একটু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে। কথা হচ্ছে, সেটির নাম অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নাকি মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল। সেটি আলোচনা হতে পারে। ডিজি (মহাপরিচালক) মেডিকেল এডুকেশন হচ্ছে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মালিক মাত্র। তিনি মেডিকেল কলেজ রেগুলেট করবেন না। বরং রেগুলেট করবেন এর বাইরের একটি বডি সেটি হচ্ছে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল।
সরকারি হাসপাতালগুলোর মালিক ডিরেক্টর হাসপাতাল। যতক্ষণ না পর্যন্ত অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বা হেলথ ফ্যাসিলিটিজ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ সেটি তিনি তদারকি করবেন। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল একই নিয়ম মেনে পরিচালিত হতে হবে। একই শর্ত মানতে পারতে হবে। রোগীকে একই মানের সেবা পেতে হবে। এক জায়গায় রাষ্ট্র বহন করবে ব্যয়, আরেক জায়গায় এনজিও এবং অন্য জায়গায় রোগী বহন করবে ব্যয়। কাঠামো তিনটি ভিন্ন হতে পারে। সরকারি হাসপাতালে রাষ্ট্র বহন করবে ব্যয়, কোনো প্রতিষ্ঠানে এনজিও শেয়ারড কিংবা দান খয়রাত করে এবং বেসরকারি পুরোপুরি লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মূল্য ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য হতে পারে কিন্তু মানে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। সরকারি কলেজ ও হাসপাতাল এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হওয়া উচিত না।
কোনো রোগী ঢাকায় অসুস্থ হওয়া এবং কুড়িগ্রামে অসুস্থ হওয়ায় কোনো পার্থক্য আছে? না নেই। ঢাকা যে মানের টেস্ট হবে, সেটিও কুড়িগ্রামে হতে হবে। কিন্তু ঢাকায় যে টেস্ট হবে সেটি মানসম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ সারা দেশের জন্য একই মানসম্পন্ন হওয়া উচিত। বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা মানসম্পন্ন হতে পারে না। তবে স্থানভেদে জমির দাম বা অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয় কমবেশি হওয়ার সঙ্গে টেস্টের মূল্যের তারতম্য হতে পারে। কিন্তু টেস্টের মানের তারতম্য হতে পারে না। জমির দাম কমবেশি হওয়ার কারণে টেস্টের মূল্যের পার্থক্য তারা রাখতেই পারে। অর্থাৎ যেখানে জমির দাম বেশি সেখানে টেস্টের দাম বেশি হোক, যেখানে কম সেখানে টেস্টের দামও কম হোক। যারা বেসরকারি হাসপাতালের মালিক তারা জানে যে ঢাকা, কুমিল্লা বা কুড়িগ্রামে হোক বিনিয়োগের পার্থক্যের কারণে মূল্য নির্ধারণে কিছু পার্থক্য হতে পারে কিন্তু মানের দিকে কোনো পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা একদম স্পষ্ট।
একইভাবে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী একটি ইতিবাচক ধারণা আছে। বাংলাদেশে ১ হাজার ৪০০ ধরনের ওষুধ আছে। এর মধ্যে ৩০০ বা তার কাছাকাছি ওষুধ হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, যা দিয়ে মোটাদাগে ৮৫ শতাংশ রোগের চিকিৎসা করা যায়। এটি ১৯৭৭ সাল থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কর্তৃক স্বীকৃত।
এ ধারণার আলোকে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের এ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্র নিতে চায়। রাষ্ট্র কি তাৎক্ষণিক পারবে? পারবে না। ধরা যাক, এখন এ ধরনের ওষুধ আছে ৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যের। কিন্তু সরকারের এ মুহূর্তে এ জায়গায় দেড় হাজার বা দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। সুতরাং বাকি মূল্যমানের ওষুধগুলো বেসরকারি খাত থেকে কিনতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলো পৌঁছে দেয়া। আর এ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই সরকার মনে করে, এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ নয় বরং মূল্য নির্ধারণ করব। মূল্য নির্ধারণ হবে একটি যৌক্তিক পদ্ধতিতে।
বিশ্বে মূল্য নির্ধারণের ৮-১২টি স্বীকৃত যৌক্তিক পদ্ধতি আছে। এ স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি আমাদের কোন ওষুধের জন্য প্রযোজ্য সেটা আমরা পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে এনে আলোচনা করেছি। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটি ওষুধ কোম্পানির মুনাফার সুযোগ, বিকাশের সুযোগ, এমনকি সীমিত আকারে গবেষণার সুযোগ, এজন্য যে ‘রিটেইলার কমিশন’ সেটা নিয়ে, বাংলাদেশের কর কাঠামোয় তার অবস্থান ও বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং মুনাফা ফেরত পাওয়ার বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
দীর্ঘদিন ধরে এমআরপি বা ইন্ডিকেটিভ প্রাইসের একটা কাঠামো ছিল, সেই কাঠামোটির আওতায় এ দেশের ওষুধ শিল্প বিকশিত হয়েছে। গত ৪২-৪৩ বছরে যাদের আগে ৫ কোটি টাকা টার্নওভার ছিল, বর্তমানে তাদের ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা টার্নওভার। এমনকি যাদের অস্তিত্ব ছিল না, বর্তমানে তাদেরও ১ হাজার ২০০ কোটি থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা টার্নওভার হয়েছে।
কোনো সরকারই চায় না একটি শিল্প কিংবা শিল্পের বিকাশ নষ্ট হয়ে যাক। কিন্তু সরকারকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। সাধারণ জনগণের প্রাপ্যতা ও শিল্পের বিকাশের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা দরকার। এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পারলে একটি অন্যায্য ব্যবস্থা তৈরি হবে। এমনকি দেশের প্রথম সারির ৫-১০টি ওষুধ কোম্পানির প্রবৃদ্ধির মাত্রা লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। আমরা বলেছি, প্রবৃদ্ধি একটি যৌক্তিক পরিসীমার মধ্যে আনতে হবে। কোনো কোম্পানির পণ্য ২০০ থেকে ৩০০ বা ৪০০ হবে, তবে সেটি কত দিনের মধ্যে হবে, সেটিও একটি বিষয়।
ওষুধের তিনটি খাতের মধ্যে একটি প্রিভেনটিভ, যার ব্যয়ের প্রায় পুরোটি রাষ্ট্র বহন করে এবং খুবই সামান্য কিছু ক্ষেত্রে এনজিওর অংশীদার আছে। প্রমোটিভ খাতের ওষুধেরও ৯০ শতাংশ ব্যয় বহন করে রাষ্ট্র, বাকিটা সবাই ব্যবহার করে। বেসরকারি খাতের অবদান হচ্ছে কিউরেটিভ কেয়ারে। মানুষের মূল খরচ হচ্ছে কিউরেটিভে। রাষ্ট্র প্রাথমিক পর্যায়ে প্রিভেনটিভ ও প্রমোটিভের সিংহভাগ ওষুধের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করছে। সেটি টিকা, ক্যাপসুল ও ভ্যাকসিন প্রভৃতি নামে।
বিএনপি যদি প্রিভেনশনে গুরুত্ব দেয় তাহলে সেটির ইতিবাচক প্রভাব পড়তে ১৫-২০ বছর সময় লাগবে। কিন্তু ১৫-২০ বছরে এই কিউরেটিভ কেয়ারের বোঝা থাকবেই আমাদের। কৌশলগত পরিকল্পনায় যারা থাকবেন, অগ্রাধিকার সরিয়ে প্রিভেনটিভে ও প্রমোটিভে বরাদ্দ বাড়ানো হবে। বর্তমানের প্রিভেনটিভ ইন্টারভেনশন কি আগামী অর্থবছরের বাজেটে কোনো প্রভাব ফেলবে? মোটেই না। বরং এটি আরো ১৫ বছর পর প্রভাব ফেলবে।
আমরা যুবককে ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ বলছি। কিন্তু প্রবীণদের বুদ্ধিমত্তাও একটি ডিভিডেন্ড। প্রবীণরা ৭০-৭৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকছেন। তার বুদ্ধিমত্তাকে রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে হবে। আবার প্রবীণরা যখন রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে যাবেন তখন রাষ্ট্রকে প্রবীণ স্বাস্থ্যের সেবা নিতে হবে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত প্রবীণদের পকেটে অনেক টাকা থাকবে। বেসরকারি খাত যদি মুনাফা লাভের আশায় যাদের বেশি অর্থ রয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বিনিয়োগ করে, তাহলে স্বাস্থ্যে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ প্রায় ১৮ কোটি মানুষের একটি বড় অংশের তেমন অর্থই নেই। সরকারকে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় সুরক্ষা দিতে হবে। সেটি কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি একটি ধারণামাত্র। যাদের অর্থ নেই, তাদেরকেই সুরক্ষা দিতে হবে রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রকে করের অর্থে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি কিছু মাত্রার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
ডিরেগুলেশন বা অনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় উদাহারণ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি কি ওষুধকে ডিরেগুলেশন করে দিয়েছে? না। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় রেফারেন্স যুক্তরাষ্ট্রের রেগুলেটরের। সংস্কার কমিশনও বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) হচ্ছে রেগুলেটর। এটি বিশ্বে মানসম্পন্ন। বিশ্বের অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির সেরা যারা, সেখানেও তারা স্বাস্থ্যকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংক কিংবা তৈরি পোশাক শিল্প অনিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য পৃথিবীর খুব কম দেশেই অনিয়ন্ত্রিত আছে।
যারা হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক বা ক্লিনিকের মালিক তারা এ দেশের নাগরিক। এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় যারা চিকিৎসাসেবা নেবেন বা ওষুধ কিনবেন তারাও এ দেশের নাগরিক। এ দেশের নাগরিক হিসেবেও একটি সীমারেখা টানতে হবে।
আমরা যারা এ পাঁচ তারকা হোটেলের ভেতরে বসে আলোচনা করছি, এ হোটেলের বাইরে থাকা মানুষের ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই? তাদের জন্য ভাবার কোনো লোক নেই? আছে। দেশের সব উন্নয়ন অর্থপূর্ণ হবে যখন মানুষ সুস্থ থাকবে। বড় বড় অবকাঠামো, বিশেষ করে বৃহৎ অট্টালিকা, মহাসড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট ও ইটপাথরের যে উন্নতি সেগুলো নিরর্থক, যদি দেশের মানুষ সুস্থ না থাকে। মানুষ যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকে তাহলে সব উন্নয়ন স্বার্থক হবে। বিনিয়োগ ব্রিজ, রাস্তা ও শিল্পে লাগবে। দিনশেষে সব বিনিয়োগ অর্থহীন যদি দেশের ১৮ কোটি মানুষ সুস্থ না থাকে। আমাদের প্রত্যাশা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সম্মানজনক হতে হবে। এটি যেন নির্যাতন ও অত্যাচারের পর্যায়ে না যায়।
দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের চিকিৎসার জন্য ৩০০ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এগুলোর দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। বাকি ১ হাজার ১০০ ওষুধ তারা তাদের নিজেদের মতো বিক্রি করতে পারবে। আমরা কখনই চাই না, উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে কোনো ওষুধ বিক্রি করা হোক। ৮৫ শতাংশ চিকিৎসার জন্য যে ওষুধগুলো লাগবে সেগুলো উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। ওষুধ শিল্প মালিকদের লাভের জন্য বাকি ১ হাজার ১০০ ওষুধ থাকল। এখন লাভ মানে কী? কত লাভকে লাভ বলা যায়? এটি চিন্তা করা উচিত। এজন্য আমি বলেছিলাম, শীর্ষ ১০টি কোম্পানির প্রবৃদ্ধির দিকে তাকালে বোঝা যাবে ‘কত লাভকে লাভ বলা যাবে। বেসরকারি খাতের উন্নতি এবং বেসরকারি খাতকে সরকারের পাশে চলার জন্য যতটুকু সহায়ক পরিবেশ দরকার ততটুকু নিশ্চিত করবে।
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান: বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
[বণিক বার্তা আয়োজিত প্রথম ‘বাংলাদেশ হেলথ কনক্লেভ ২০২৫’-এ বিশেষ অতিথির বক্তৃতায়]