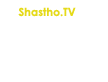সাক্ষাৎকার
চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে রেফারেল সিস্টেম চালু করতে হবে : অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান

বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেট বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যকে এশিয়ার বিস্ময় বলে চিহ্নিত করেছে। অথচ উল্টোদিকে দেশের চিকিৎসাসেবা নিয়ে আস্থার সংকটও রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা নিয়ে বরাবরই অভিযোগ থাকলেও, করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার লাভের পর থেকেই দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থা যে কতটা নাজুক, সেই চিত্রটি ফুটে উঠেছে।
গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন বিশিষ্ট ওষুধবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ফার্মাকোলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ ফার্মাকোলজিক্যাল সোসাইটির চেয়ারম্যান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুহাম্মদ ওয়াশিকুর রহমান।
বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেট বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যকে এশিয়ার বিস্ময় বলে চিহ্নিত করেছে; কিন্তু চিকিৎসাসেবা নিয়ে মানুষ খুশি না, আবার আস্থার সংকটও দেখি। আপনার মূল্যায়ন কী?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান: ল্যানসেটে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সাফল্য সম্পর্কে মূলত যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে সেগুলো হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা খাত, যেমন- ইপিআই, জন্মনিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু মৃত্যুর হার, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে প্রসব ইত্যাদি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং সে কারণে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাগুলো নিয়ে তেমন বড় ধরনের অসন্তোষ নেই। মানুষের অসন্তোষ শুরু হয় যখন তিনি হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করার জন্য আসেন। তাদের আস্থাহীনতার জায়গাটি চিকিৎসাসেবাকে ঘিরে অর্থাৎ যখন তিনি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কিংবা আউটডোরে চিকিৎসা নিতে আসেন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য যে অবকাঠামো ও লোকবল প্রয়োজন হয়, ধারাবাহিক এবং পরিকল্পনামাফিক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের অভাবে তা কখনোই পূরণ করা হয়নি। প্রতিদিন একটি উপজেলায় আউটডোরে গড়ে ৪শ’ এবং মেডিকেল কলেজ বা সমপর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ৪ থেকে ১২ হাজার রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই হাসপাতালে এত অল্পসংখ্যক চিকিৎসক দিয়ে এত বেশিসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করা হয় না। এই অবকাঠামো ও জনবল দিয়ে রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদান সম্ভব নয়। এখানে বুঝতে হবে যে প্রথমত সরকারি হাসপাতালগুলোতে সত্যিকারের প্রয়োজনের তুলনায় সরকার অনেক কম চিকিৎসক, নার্স বা সহায়ক কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি যেমন- ওষুধ এবং রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জামাদি-কেমিক্যাল-রি-এজেন্টের সরবরাহ এবং জরুরি বিভাগের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো কম বিনিয়োগ করেছেন। ফলে একজন সরকারি চিকিৎসক যদিও প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন, অথচ সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাবে অধিকাংশ রোগীই সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। কারণ এই বিপুলসংখ্যক রোগীর জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমন ওষুধ, ল্যাবরেটরি টেস্ট বা এক্স-রে বা হাসপাতালের বেড এর ব্যবস্থা করতে পারেনি। চিকিৎসার খরচের শতকরা ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ জনগণকে তার নিজের পকেট থেকেই বহন করতে হয়। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদিতে বরাদ্দ কম দেওয়ার ফলে সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত ওষুধ ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার চাহিদা তৈরি করছে আর বেসরকারি খাত তা মুনাফার বিনিময়ে পূরণ করছে। অর্থাৎ খেয়াল করবেন যে রোগীদের অসন্তোষ যেসব বিষয়াদিকে ঘিরে, সেগুলো মূলত সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ অপ্রতুলতা বা অগ্রাধিকারের সংকট। আর একটা কথা দুঃখ নিয়েই বলতে হয় যে এত অপ্রতুলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এদেশের চিকিৎসকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাকর্মীরা যে প্রচণ্ড চাপ নিয়ে সেবা প্রদান করছেন, এদেশের মিডিয়া বা সাধারণ মানুষের কাছে সেটি যথাযথভাবে সম্মানিত বা প্রশংসিত হচ্ছে না। এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। আমি এ প্রসংগে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আপনারা খেয়াল করবেন যে তিনি বাংলাদেশের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি স্পষ্টভাবে তার নিজের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ও চলমান মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশি চিকিৎসক এবং নার্সদের অবদানের জন্য আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
বাংলাদেশে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসাসহ নানা ধরনের অভিযোগ শোনা যায়? এই সমস্যার সমাধানে করণীয় কী?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : প্রথমত, চিকিৎসার ভুলটা ধরছেন কে? তিনি কি চিকিৎসক? চিকিৎসক অথবা চিকিৎসাদানের স্বীকৃত দক্ষতা নেই এমন কারো পক্ষে কি চিকিৎসার ভুল ধরা সম্ভব? মোটেই না। মনে রাখা দরকার যে পেশাগত ভুলের সঙ্গে অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা অনৈতিক আচরণকে গুলিয়ে ফেলাটাও সঠিক কাজ নয়। পেশাগত ভুলের বিষয়ে সাধারণভাবে দেশের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এর কাছে অভিযোগ করাটাই বিশ্বে স্বীকৃত পদ্ধতি। পৃথিবীর যে সকল দেশে রোগ নির্নয়ের সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা প্রদান করেন তেমন দেশেও (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) গবেষণায় দেখা যায় যে প্রতি বছর ৪৮ হাজার থেকে ৯৮ হাজার জন রোগী চিকিৎসার ভুলে মৃত্যুবরণ করেন। খেয়াল করবেন যে এটাকে তাঁরা বলছে মেডিকেল এরর (Medical Error)। তাই আমি বলব যে বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক রোগীর চাপ এবং সীমিত রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগের মধ্যে যেভাবে চিকিৎসকদের চিকিৎসাসেবা দিতে হয়, দেশের সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া সেগুলোর উন্নতি করা বেশ কঠিন বা দুঃসাধ্য।
অন্য যে বিষয়টি বললেন সেটি হচ্ছে নীতি নৈতিকতার বিষয়। এ প্রসংগে বলতে চাই যে একসময় এদেশে পড়াশোনার একেবারে প্রথমদিকেই আদর্শলিপি পড়ানো হতো। তাতে সমাজে যে মূল্যবোধের চর্চা হতো সেটার কারণে দুর্নীতিবাজরা বা তাদের সন্তানরা লজ্জায় আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের কাছে মুখ দেখাতে পারতো না। দুর্নীতির টাকা দিয়ে কেউ লোক দেখানো কিছু করতে লজ্জা পেত বা দ্বিধায় থাকত, অর্থাৎ সেটা একটা সামাজিক লজ্জার বিষয় ছিল। অথচ আজকের অবস্থাটা অনেকখানিই ভিন্ন বা বলতে পারেন উল্টো। যখন কোন সমাজ একজন সৎভাবে জীবনযাপন করা চিকিৎসক অথবা একজন সৎ ও যোগ্য শিক্ষককে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে অর্থবিত্ত, জাঁকজমক বা প্রভাব প্রতিপত্তির ওপর নির্ভর করে কাউকে প্রাধান্য দিচ্ছে, সেই সমাজে নীতিনৈতিকতা আশা করেন কীভাবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৈতিকতা ও আদর্শ শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিকভাবেও নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। অনিয়ম বা অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক চাপ তৈরি করতে পারলেই শুধু এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন যে একজন চিকিৎসকের কাছে নৈতিকতার উচ্চমান আশা করা হয়, আশা করা হয় যে তিনিই সমাজে ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করবেন। এই কথাটার সঙ্গে আমিও একমত কিন্তু একইসঙ্গে সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা খাতে নৈতিকতার উচ্চমান বজায় রাখা যে বেশ কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং সেটাও সত্য।
বাংলাদেশ তার নিজস্ব প্রয়োজনের ৯৭ শতাংশ ওষুধই দেশে উৎপাদন করছে; কিন্তু গবেষণা খুব একটা দেখছি না, এতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে কি-না?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : এক কথায় বললে বাংলাদেশ ওষুধে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু এটা বুঝতে পারা জরুরি যে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এখনো মূলত ফরমুলেশন শিল্পের পর্যায়ে রয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষুধের কাঁচামাল এবং প্যাকিং সামগ্রী আমদানি করে দেশে শুধু ফিনিশড প্রোডাক্টটি তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে অল্প কয়েকটি ওষুধেরই কাঁচামাল এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়েল দেশে উৎপাদিত হয়। এতদিন যাবৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইন (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্যাটেন্টভুক্ত ওষুধ কোনো রয়্যালিটি না দিয়ে উৎপাদনের সুযোগ পাচ্ছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ হিসেবে মাথাপিছু আয়ের হিসেবে আমরা নিম্ন-মধ্যম স্তরে উন্নীত হয়েছি বিধায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই TRIPS-এর এই সুবিধাটি থেকে বঞ্চিত হবো। তখন আমাদের নতুন আবিষ্কৃত ওষুধ, অর্থাৎ প্যাটেন্ট অন্তর্ভুক্ত ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল উৎপাদকের কাছ থেকে রয়্যালটি দিয়ে অনুমতি নিয়ে উৎপাদন করতে হবে। ফলে ধারণা করা হয় যে তখন প্রায় একশ বা ততোধিক ওষুধের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সে লক্ষ্যে আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি প্রয়োজন।
এবার ওষুধ গবেষণা বা আবিষ্কারের প্রসংগে কিছু কথা বলি। মনে রাখা দরকার যে এই মুহূর্তে বিশ্বে যত ওষুধ আছে তার প্রায় ৯৯ ভাগই হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার। চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারতসহ এশিয়ার সকল দেশ মিলিয়ে ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অবদান মাত্র ১ শতাংশের চেয়েও কম। এ প্রসংগে আমি আরো একটা বিষয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, লক্ষ্য করবেন যে ওষুধ আবিষ্কারের পুরো পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটা ধনী ও বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশ ও কোম্পানিগুলো ইচ্ছা করেই অনেক জটিল এবং ব্যয়বহুল করে রেখেছে। ফলে সেটি অনুসরণ বা অর্জন করা আমাদের মতো দেশগুলোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব; কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়েই আমাদের কৌশল হওয়া উচিত ছিল ওষুধের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিশ্বের চলমান ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলোতে যুক্ত হওয়া। এর মাধ্যমে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের উদ্যোগগুলোয় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে এদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে অগ্রসর তে পারতেন। তবে একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলাদেশের মানুষের রোগ-ব্যাধি নিয়ে এদেশীয় গবেষকদের জন্য ল্যাবরেটরি অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, প্রয়োজনীয় সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞানীদের সম্মান ও উৎসাহ দানের সংস্কৃতি চালু করার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বিজ্ঞানমনষ্ক হিসেবে গড়ে তোলাটাও জরুরি।
প্রতিষ্ঠান ভেদে একই ওষুধের দামের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। ওষুধের মাননিয়ন্ত্রণ নিয়ে মানুষের মধ্যে কিছু নেতিবাচক ধারণা দেখি, এসব বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : বাংলাদেশে প্রায় ১৩০০ ওষুধ তৈরি হয়, যার মধ্যে ১১৭টি ওষুধের মূল্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো নিজেরাই মূল্য নির্ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে মানুষের মনে অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে যে জিনিসের দাম বেশি সেটির মান ভালো বলেই একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে। দাম পার্থক্যের সুযোগ থাকায় সেই ধারণাকে পুঁজি করে ওষুধের বাজারের ক্ষেত্রেও ভালো ব্র্যান্ড মানে ভালো ওষুধ, এরকম একটি বাজারকেন্দ্রিক অবৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মধ্যে এই ধারণাটি সৃষ্টি করা গেছে যে বড় কোম্পানির ওষুধ বা বেশি দামি ওষুধ মানেই ভালো, অথচ যেটির পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বা যেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। মূল্য পার্থক্যের ফলে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যেটি ওষুধ বাজারে অনৈতিক প্রবণতার চর্চা করার সুযোগ তৈরি করে।
মানের বিষয়ে বলতে গেলে বলব যে প্রতিটি রাষ্ট্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে নিজস্ব ওষুধশিল্পের অগ্রগতি, নিয়ন্ত্রকের ল্যাবরেটরি অবকাঠামো, জনবলের দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় দেড় শতাধিক দেশে ওষুধ রপ্তানি করে এবং সেক্ষেত্রে রপ্তানির শর্ত হিসেবে সবাইকে ঐসব দেশে বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে বায়োইকুইভ্যালেন্স (Bioequivalence) পরীক্ষার ফলাফল জমা দিতে হয়। যে সকল কোম্পানি উন্নত দেশগুলোতে ওষুধ রপ্তানি করেন, তারা সাধারণত বিদেশের কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এই পরীক্ষাটি করিয়ে আনেন; কিন্তু দুঃখজনক সত্যটি হলো, ওষুধ খাতে এত সমৃদ্ধি অর্জনের পরও এখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য বায়োইকুইভ্যালেন্স পরীক্ষাটি আইনত বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত ওষুধের ক্ষেত্রে সেটি মেনে চলার ব্যাপারে একটু উদাসীনতা আছে। আমার মনে হয় মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যাদের ওষুধের মাননিয়ন্ত্রণ, বিশেষত বায়োইকুইভ্যালেন্স পরীক্ষার সামর্থ্য আছে তাদের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে সবাই মিলে সার্বিকভাবে দেশের ওষুধের মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব।
অনেকেই বলছেন যে করোনা মহামারির চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এবং সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এই সংকট মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : অনেকেই এটা মনে করেন যে এই মহামারি চলমান থাকা অবস্থায় বা শেষ হওয়ার পরপরই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এর মহামারি পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলবে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক ওষুধের দোকান থেকে প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০ লাখ মানুষকে কোনো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অপ্রয়োজনে বা ভুলভাবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করবেন এটা কিন্তু বাংলাদেশের মাত্র এক দিনের চিত্র। যদিও ইতোমধ্যে দেশে সীমিত আকারে কিছু মডেল ফার্মেসি চালু হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সারাদেশের ওষুধের দোকানগুলোকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ঢাকাতেই এগুলোকে নজরদারিতে রাখা যাচ্ছে না, আর ঢাকার বাইরে তো দূরের কথা।
এ ছাড়াও পশুসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি খাতেও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। দেশের অধিকাংশ মুরগির খামারগুলোতে প্রতিদিন সকালে পানির সঙ্গে প্রায় ১৫ কোটি মুরগিকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মুরগি পালনের মাধ্যমে এই ধরনের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার পুরোটাই এড়ানো সম্ভব।
এবার একটু এই মহামারির প্রথমদিকের কথা মনে করার চেষ্টা করেন। সবাই প্রথম থেকেই জানতেন যে কোভিড একটি ভাইরাসবাহিত রোগ, কিন্তু লাখ লাখ মানুষ এন্টিবায়োটিক অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ানাশক ওষুধ খেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি আমাদের দেশেও হাসপাতালে ভর্তিকৃত কোভিডাক্রান্ত রোগীর শতকরা মাত্র ৮ থেকে ১৫ ভাগ এর ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন ছিল। ফলে বুঝা যাচ্ছে যে এই মহামারি চলমান অবস্থায় বিশ্বজুড়ে যেভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে যে ব্যাকটেরিয়াটির অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল আরো পাচ বছর পরে, সেই ঘটনাটি এখন এগিয়ে এসে হয়তো দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ঘটে যাবে।
নিজে নিজে বা অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না, কারণ এটা হয়তো আপনাকে বর্তমানে কিছু সাময়িক সুবিধা দিচ্ছে, কিন্তু আপনার সন্তান অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রজন্মেকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। সাধারণ মানুষ যদি এ বিষয়ে নিজে থেকেই সতর্ক হয়ে যায়, তাহলে ওষুধের দোকানদারেরা চেষ্টা করলেও নাগরিকদের সচেতনতার মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের অযৌক্তিক ব্যবহার কমিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব। প্রকৃত বিবেচনায় যে দোকানদার অল্প কিছু মুনাফার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করছে সে তো জানেই না যে এটা তাকে বা তার সন্তানকেও আগামীতে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অতএব, সমগ্র জাতিকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। সাধারণ মানুষকে অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল অ্যান্টিবায়োটিকের প্যাকেট এবং স্ট্রিপের রং লাল করা হলে তা সহজেই সকলকে সতর্ক আচরণ করতে সাহায্য করবে।
এ প্রসংগে বলা ভালো যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলোর প্রয়োগ খুবই কম।
মেডিকেল কলেজসহ দেশে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; কিন্তু অনেকের অভিযোগ আমরা প্রচুর প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি কিন্তু মানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : বেশ আগেই স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অভাব চিহ্নিত হয়েছিল এবং সেটি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা শুরু হয়েছিল। এর ফলে আপাতত সংখ্যার দিক থেকে সক্ষমতার সম্প্রসারণ হলেও এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি ও দক্ষ জনবলসহ আনুষঙ্গিক দিকে তেমন কোনো নজরদারি করা হয়নি। আমি মনে করি যে চিকিৎসা শিক্ষার মান রক্ষায় প্রধান রক্ষাকবচটি হলো ভালো শিক্ষক; কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি হলো যে ভালো মানের শিক্ষক তৈরি করা হয়নি বা যায়নি এবং ফলে চিকিৎসাসেবায় এটার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এ প্রসংগে আরো লক্ষ্যণীয় যে চিকিৎসাক্ষেত্রে শিক্ষকতা এখনো এদেশে কোন আকর্ষণীয় পেশা হয়ে উঠছে না, বিশেষত চিকিৎসা পেশার তুলনায় শিক্ষকতা এখনো অনেক কম আকর্ষণীয়।
বাংলাদেশ একসময় ভ্যাকসিন তৈরি করত। কিন্তু আমরা করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে পারলাম না কেন? এখন আমাদের সক্ষমতা কতটুকু আছে?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : ভ্যাকসিন উৎপাদনে আমাদের যে সামর্থ্যটা ছিল, সেটি বিসর্জন দেওয়া আমাদের নীতিনির্ধারকদের একটা কৌশলগত ভুল বলেই আমার মনে হয়। করোনার টিকা উৎপাদনের ব্যাপারটা আসলে ভূরাজনৈতিক বিষয়, শুধু বিজ্ঞানের নয়। আমি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাই না, শুধু বলব এখন সরকার দেশে টিকা উৎপাদনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেটা খুবই ইতিবাচক। তবে এক্ষেত্রে সরকার কোন ধরনের ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট বসানোর চিন্তা করছে, সেটা দেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ভ্যাসকিন উৎপাদনের প্ল্যান্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, অতএব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহল তথা বিজ্ঞানীদের মতামত নেওয়াটা উত্তম হবে। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ভ্যাকসিন উৎপাদনে সমর্থ প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করাই উচিত হবে।
বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় অন্যান্য খাতের তুলনায় স্বাস্থ্য খাত বাজেটে বরাবরই কম গুরুত্ব পেয়েছে। এটাই কি স্বাস্থ্য খাতের নাজুক পরিস্থিতির জন্য দায়ী?
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : হ্যাঁ, জাতীয় প্রবৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য খাতের অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে যেটি স্বাস্থ্য খাতের নাজুক অবস্থা তৈরি হওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ। তবে শুধু বাজেটের পরিমাণগত বরাদ্দই নয়, খাতভিত্তিক বরাদ্দের সফল ব্যবহার এবং আর্থিক অব্যবস্থাপনার বিষয়েও উন্নতির লক্ষ্যে নজরদারি রাখা দরকার।
বিগত ৫০ বছরের স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন জানতে চাই।
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান : আমরা একটি লড়াকু জাতি এবং যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সমস্যায় আমরা লড়াই করে জিতে যাই। শুধু লড়াই করার সামর্থ্যরে অভাবে বিশ্বে অনেক জাতি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি বা মহামারিতে কাবু হয়েছে; কিন্তু যথেষ্ট গবেষণার অভাবে এতদাঞ্চলের মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে তেমন কিছুই আমরা জানি না। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে পারলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হতো এবং সেটা বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের জন্যও একটি সম্ভাবনাময় বিষয় বলে বিবেচিত হতো। গত বছর স্বাস্থ্য খাতে সমন্বিত গবেষণার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেটি এযাবৎকালে গবেষণা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। আশা করা যায় এর ফলে দেশের স্বাস্থ্য খাতের গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় একটা নতুন গবেষণা সংস্কৃতির সৃষ্টি হবে।
বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তেমন কোনো সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে জরুরি সেবা মারাত্মকভাবে অবহেলিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় ৭০টির মতো শাখায় দেশে ডিগ্রি চালু আছে, কিন্তু ইমার্জেন্সি মেডিসিন নিয়ে কোনো কোর্স আজ অবধি চালু করা হয়নি; কিন্তু আমরা জানি যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান জরুরি চিকিৎসাসহ সার্বিক চিকিৎসাক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক, প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক এবং প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে পারলেই এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর শুরু হবে।
আউটডোরভিত্তিক চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই রেফারেল সিস্টেম চালু করতে হবে। দুনিয়াজোড়া রেফারেল সিস্টেম এর বিভিন্ন ধরনের মডেল আছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের জন্য একটি যথাযথ ও বাস্তবানুগ রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হলে সাধারণ মানুষ পর্যায়ক্রমে চিকিৎসাসেবায় সন্তুষ্ট বোধ করবেন এবং আউটডোর সেবায় অভাবনীয় উন্নতি দেখতে পারবেন।
আপনাকে ধন্যবাদ।
অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।